এমপিওভুক্ত শিক্ষার একাল ও সেকাল
- Update Time : শনিবার, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪
- ১৯ Time View

বাংলাদেশে এমপিওভুক্ত (Monthly Payment Order) শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে, একালের ও সেকালের এমপিওভুক্ত শিক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রাথমিক এবং বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।
শুরুর ইতিহাস:
এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা মূলত ১৯৮০-এর দশকে, যখন সরকার শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমকে টেকসই করার উদ্যোগ নেয়। প্রথম দিকে এমপিওভুক্তি প্রক্রিয়া ছিল সীমিত এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক এই সুবিধা পেতেন। এই উদ্যোগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল:
- গ্রামীণ ও শহরতলির এলাকায় শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি।
- বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মান উন্নত করা।
- শিক্ষকদের পেশাগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।
প্রথম দিকে, প্রক্রিয়াটি ছিল ধীর এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রভাব ও পক্ষপাতিত্বের কারণে জটিল। তদারকির অভাবে অনেক সময় এই সুবিধার যথাযথ প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হত। কিন্তু ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে, এবং ১৯৯০-এর দশকে এটি আরও সংগঠিত রূপ পায়।
সেকালের এমপিওভুক্ত শিক্ষা:
১. নিয়ম-কানুন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া:
- এমপিওভুক্তির প্রক্রিয়া ছিল ধীরগতি ও জটিল।
- প্রশাসনিক দক্ষতার অভাবে অনেক সময় এমপিওভুক্তির জন্য বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হতো।
- যোগ্যতার মানদণ্ড এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্রে অস্পষ্টতা থাকায় অনিয়ম দেখা দিত।
২. শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা:
- এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা সময়মতো বেতন পেতেন না।
- বেতন কাঠামো ছিল নিম্নমানের, যা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত ছিল না।
- অন্যান্য আর্থিক সুবিধা, যেমন পেনশন বা উৎসব ভাতা প্রায় অনুপস্থিত ছিল।
৩. প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান:
- এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল সীমিত।
- গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থা ছিল অবহেলিত।
- অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও শিক্ষার মান নিম্নপর্যায়ে ছিল।
৪. সরকারি নজরদারি:
- সরকারি তদারকি ছিল খুবই সীমিত।
- অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠত।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব ছিল প্রকট।
৫. শিক্ষার্থীদের অবস্থা:
- শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য পর্যাপ্ত উদ্যোগ ছিল না।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি এবং ফলাফল অনেক ক্ষেত্রে সন্তোষজনক ছিল না।
একালের এমপিওভুক্ত শিক্ষা:
১. নিয়ম-কানুন ও আধুনিকায়ন:
- বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষার প্রক্রিয়া অনেক বেশি নিয়মতান্ত্রিক এবং দ্রুততর।
- তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে, যেমন অনলাইন আবেদন ও ডাটাবেজ ব্যবস্থাপনা।
- যোগ্যতার মানদণ্ড কঠোরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যা দক্ষ শিক্ষকদের অগ্রাধিকার দেয়।
২. শিক্ষকদের আর্থিক উন্নতি:
- মাসিক বেতন দ্রুত বিতরণ করা হয়, যা আগের তুলনায় অনেক বেশি সুশৃঙ্খল।
- বেতন কাঠামো উন্নত হয়েছে এবং শিক্ষকদের উৎসব ভাতা, পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়।
৩. প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান:
- এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টা রয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও ফলাফলে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
৪. সরকারি নজরদারি ও স্বচ্ছতা:
- প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে সরকারি তদারকি অনেক বেড়েছে।
- নীতিমালা লঙ্ঘন করলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
- তথ্য ডিজিটালাইজেশনের ফলে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়েছে।
৫. চ্যালেঞ্জ:
- নতুন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তির জন্য প্রতিযোগিতা বেড়েছে।
- অনেক সময় রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে এমপিও প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি হয়।
- শিক্ষার মান বজায় রাখা এবং শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন এখনও বড় চ্যালেঞ্জ।
৬. শিক্ষার্থীদের উন্নতি:
- শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পদ্ধতিগত শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে।
- ফলাফলে স্বচ্ছতা এবং শিক্ষকদের দিকনির্দেশনার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
তুলনামূলক বিশ্লেষণ:
| বিষয় | সেকাল | একাল |
|---|---|---|
| প্রক্রিয়ার গতি | ধীর ও জটিল | দ্রুত ও সহজ |
| শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা | নিম্নমানের | উন্নত ও স্থিতিশীল |
| প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও মান | সীমিত ও দুর্বল | উন্নত ও বিস্তৃত |
| সরকারি নজরদারি | সীমিত | শক্তিশালী ও স্বচ্ছ |
| প্রযুক্তির ব্যবহার | অনুপস্থিত | ব্যাপক |
সারমর্ম:
এমপিওভুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে সেকাল এবং একালের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। সেকালের চ্যালেঞ্জ ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এখনকার প্রক্রিয়া অনেক উন্নত, দ্রুত এবং স্বচ্ছ। তবে, এখনও কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যেমন শিক্ষার মানোন্নয়ন, নতুন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি এবং রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত প্রশাসন। ভবিষ্যতে আরও আধুনিক এবং কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।



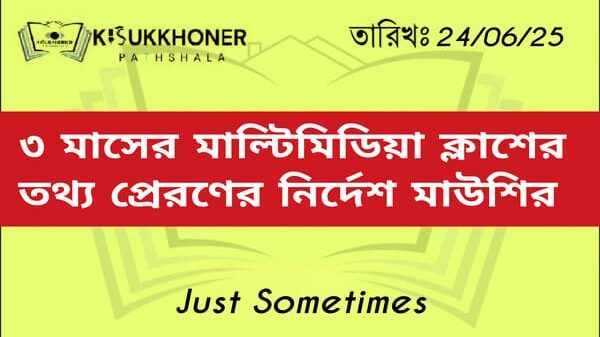
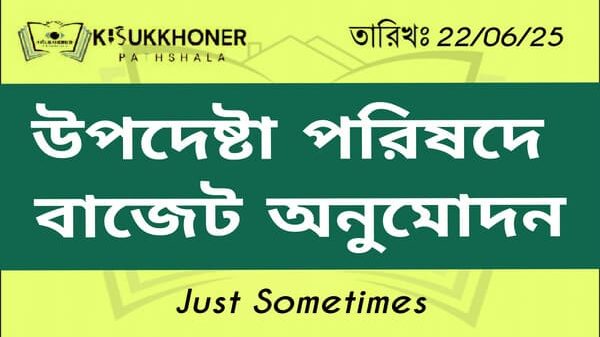


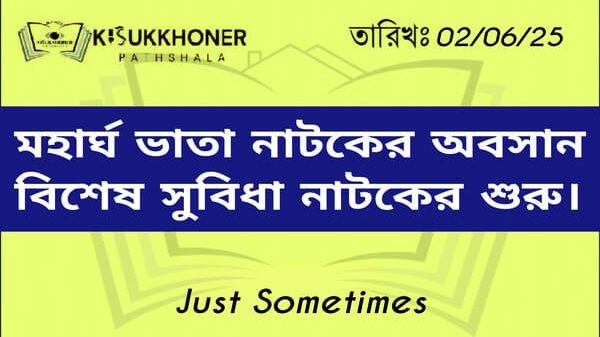
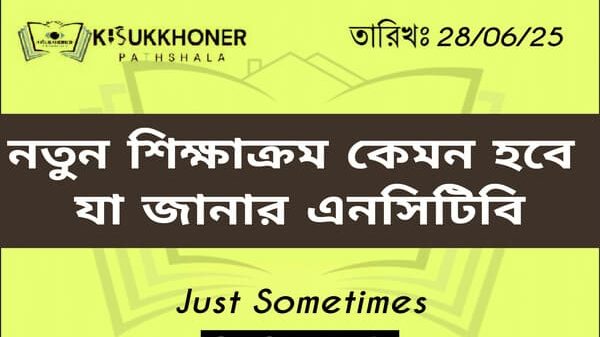
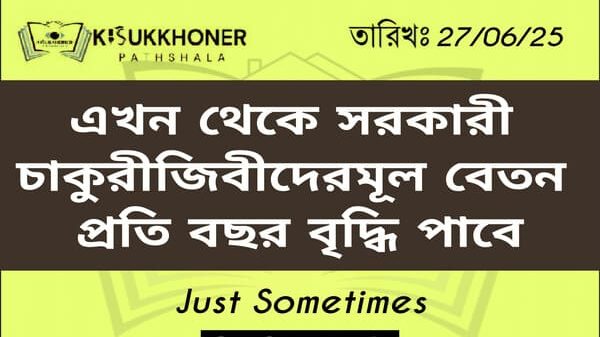
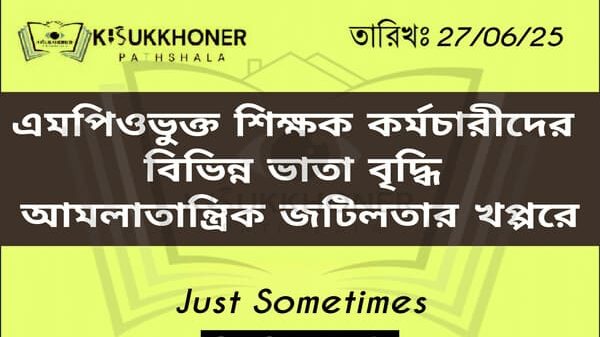
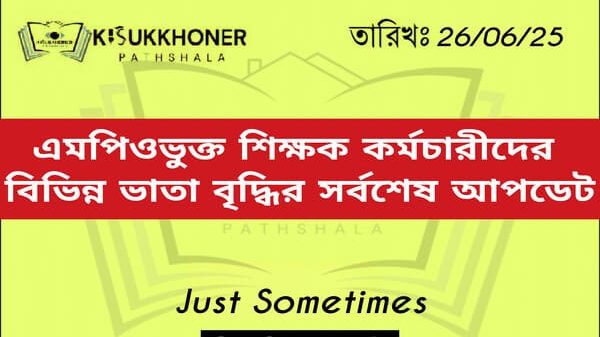
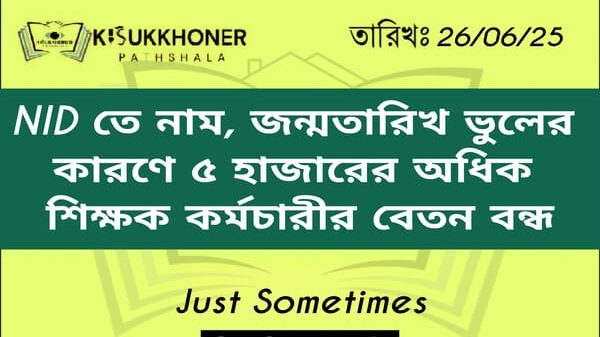
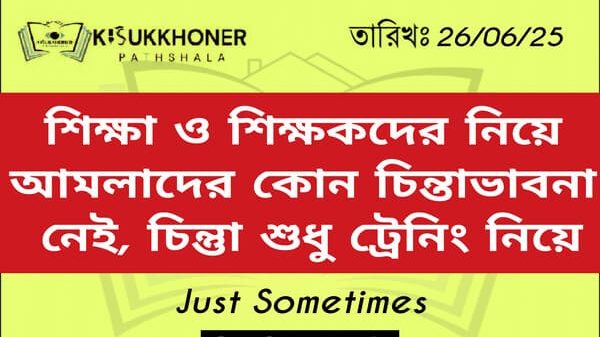
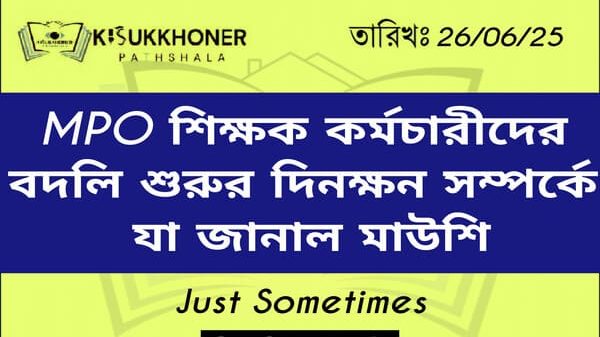
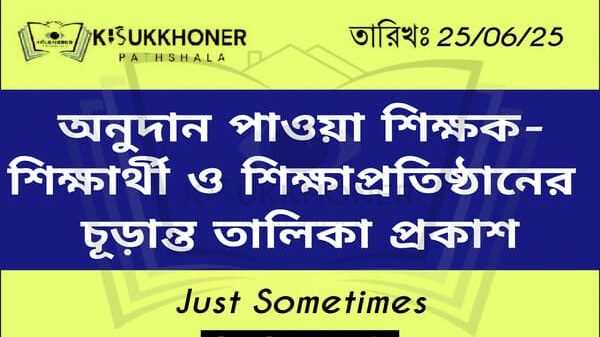
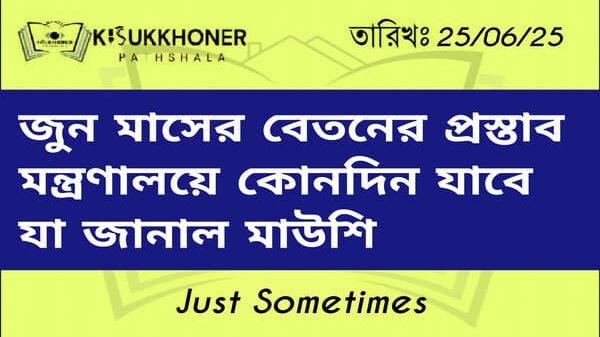
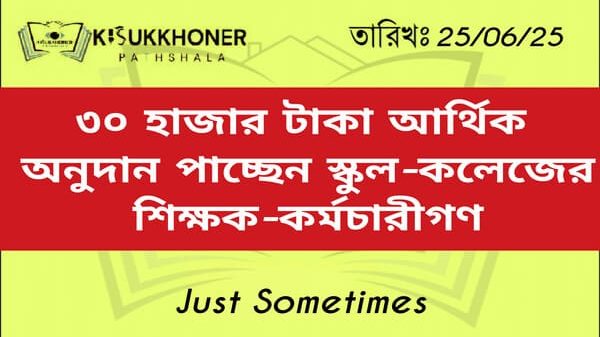
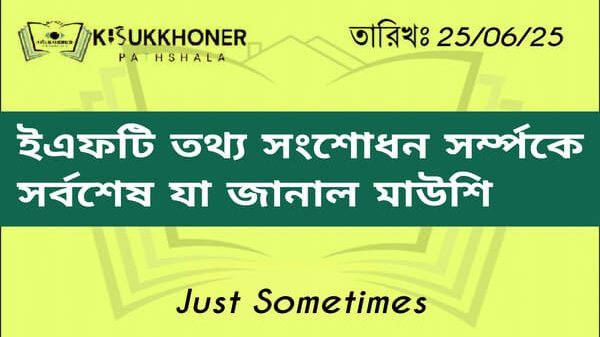
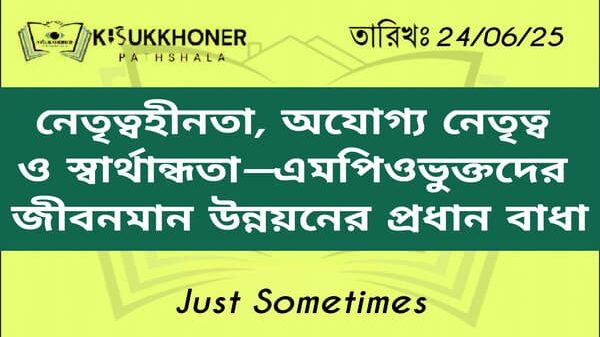
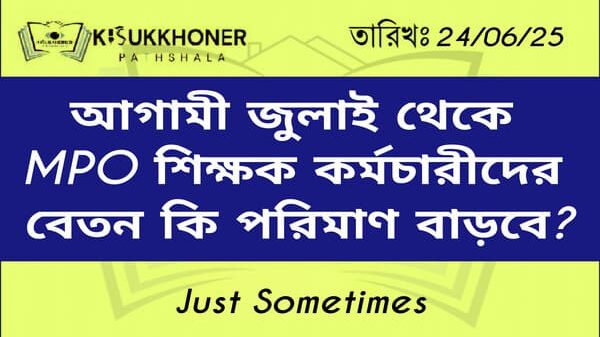
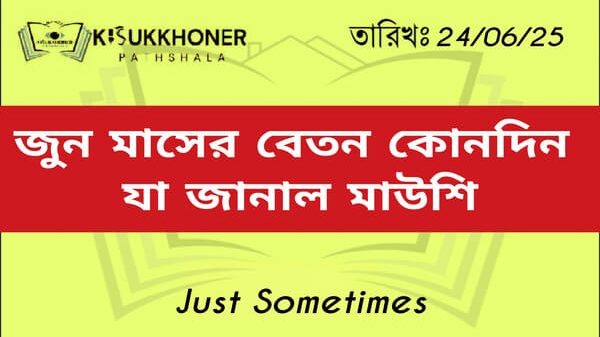
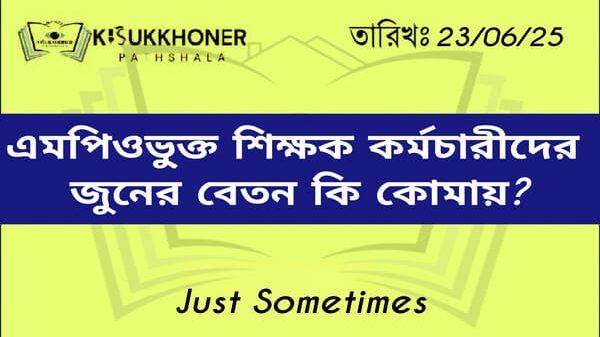
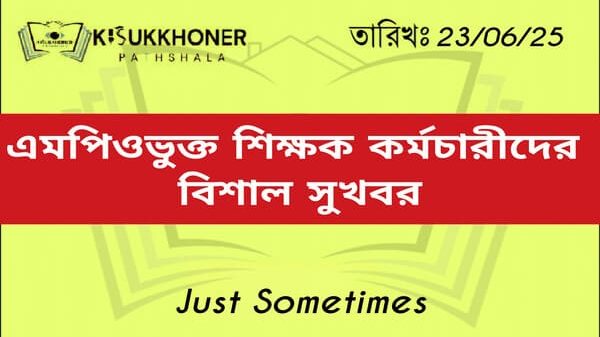
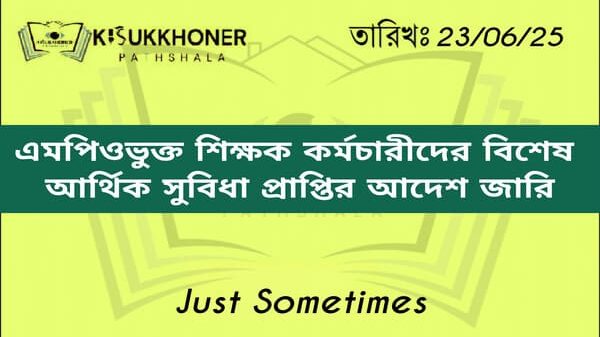
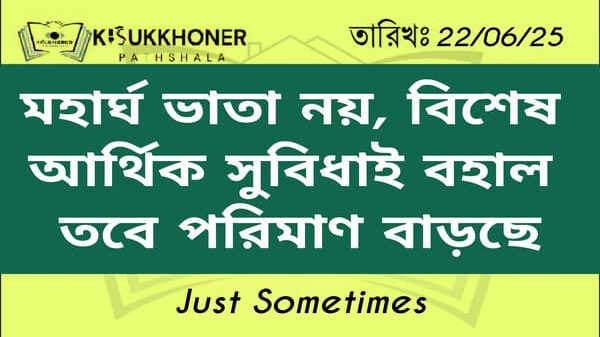
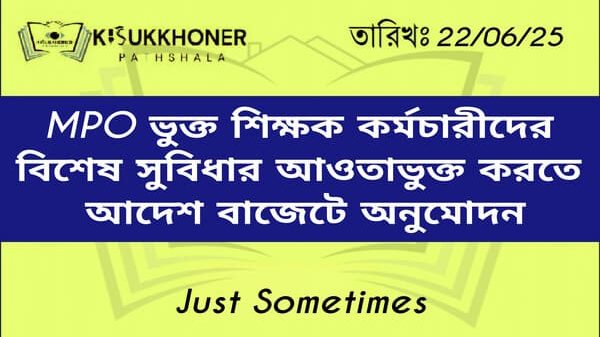
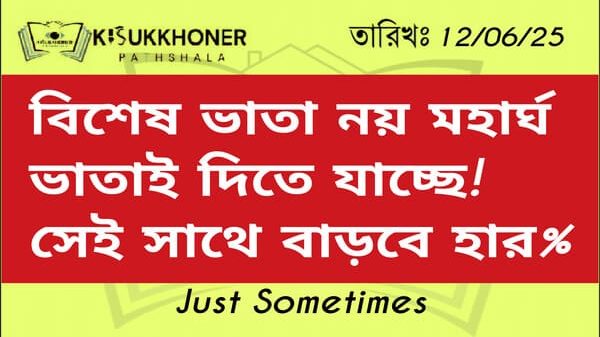
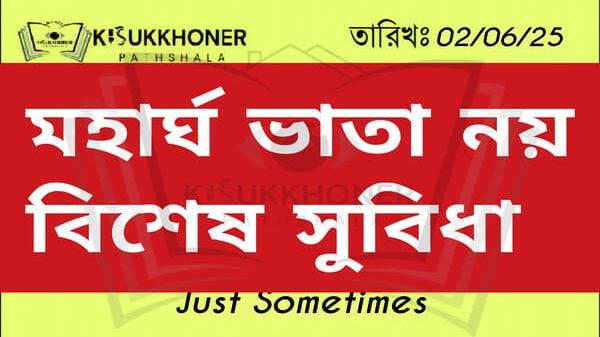
Leave a Reply