এমপিওভুক্ত শিক্ষার ইতিহাস
- Update Time : বুধবার, ৭ মে, ২০২৫
- ৩৯৬ Time View

বাংলাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস মূলত স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে গড়ে উঠতে শুরু করে। এটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ই শুধু নয় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মুল কাঠামো হলো এই এমপিওভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা। এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার শতকরা ৯৭ থেকে ৯৮ ভাগ শিক্ষার্থী এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করে থাকে। এদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে যাদের এতবেশি অবদান সেই সকল প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। স্বাধীনতার ৫৪ বছর পার হয়ে গেলেও এখনও এমপিওভুক্ত শিক্ষার স্বাবলম্বিতা এদেশের কোন সরকারই তেমন কোন ভুমিকা গ্রহণ করেনি। যদিও সেক্ষেত্রে শুধু এদেশের রাজনীতিবিদদের দোষ খুঁজে লাভ নেই, দোষ তাদের পাশাপাশি এই শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে জড়িত কতিপয় কিছু স্বার্থনেষী শিক্ষক কর্মচারীরাও এর সাথে জড়িত।
বাংলাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস: একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র
‘এমপিও’ কী?
এমপিও (MPO) অর্থাৎ Monthly Payment Order—একটি সরকার অনুমোদিত অর্থনৈতিক সহায়তা পদ্ধতি যার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সরকারি কোষাগার থেকে প্রদান করা হয়।
শুরুর পটভূমি (১৯৭১-১৯৭৮)
স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। সে সময় দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল বেসরকারিভিত্তিক, এবং শিক্ষকরা ন্যূনতম বেতনে কাজ করতেন।
🔹 ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয় (ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন)। এই কমিশনের রিপোর্টে বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সরকারি সহায়তার কথা বলা হয়।
🔹 এরপর সরকার কিছু নির্বাচিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে আংশিক বেতন ভাতা দিতে শুরু করে—এটাই পরবর্তী এমপিও নীতির ভিত্তি তৈরি করে।
এমপিও ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক সূচনা (১৯৭৮)
🔹 স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়। সে সময় দেশের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল বেসরকারি এবং শিক্ষকরা অল্প বেতনে মানবেতর জীবনযাপন করতেন। ১৯৭৩ সালে গঠিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করে শিক্ষকদের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণের। এরপর ১৯৭৮ সালে তৎকালীন সরকার এমপিও পদ্ধতি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করে, যার আওতায় বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা প্রদান শুরু হয়।
🔹 এমপিওভুক্তির মানদণ্ড ছিল:
- নির্দিষ্ট শিক্ষার্থী সংখ্যা
- পরীক্ষার ফলাফল
- অবকাঠামোগত ব্যবস্থা
- সংশ্লিষ্ট বোর্ডের অনুমোদন
এটি বেসরকারি শিক্ষকদের মাঝে স্থায়িত্ব, সম্মান এবং আর্থিক নিরাপত্তা নিয়ে আসে।
নব্বইয়ের দশক ও বিস্তার (১৯৯০–২০০০)
🔹 ১৯৯০-এর দশকে দেশে শিক্ষা বিস্তারে জোর দেওয়া হয়, ফলে হাজার হাজার নতুন বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা গড়ে ওঠে।
🔹 এই সময়ে ব্যাপক সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়। তবে যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়া অনেক প্রতিষ্ঠান এমপিও পেয়ে যায়, যার ফলে:
- বাজেটের ওপর চাপ পড়ে
- কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও ওঠে
🔹 ১৯৯৫ সালে প্রথমবারের মতো শিক্ষা মন্ত্রণালয় “এমপিও নীতিমালা” প্রণয়ন করে, যাতে যোগ্যতার ভিত্তিতে এমপিওভুক্তির শর্ত নির্ধারণ করা হয়।
সংস্কার ও স্থগিতাদেশ (২০০১–২০১০)
🔹 ২০০৫ সাল নাগাদ এমপিও বাবদ সরকারি ব্যয় দ্রুত বাড়তে থাকে। এই সময়ে সরকার বিভিন্ন সময় নতুন এমপিও স্থগিত করে।
🔹 ২০০৮ সালের পর থেকে দীর্ঘ সময় নতুন কোনো প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়নি। ফলে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী বছরের পর বছর বিনা বেতনে কাজ করতে থাকেন।
পুনঃচালু ও ডিজিটালাইজেশন (২০১০–২০২৩)
🔹 ২০১০ সালে শেখ হাসিনা সরকার আবারো এমপিও প্রক্রিয়া চালু করার উদ্যোগ নেয়।
🔹 ২০১৩, ২০১৮ ও ২০২১ সালে ধাপে ধাপে কিছু প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে এমপিওভুক্ত করা হয়।
🔹 ২০২৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আইবাস++ সফটওয়্যার ও ইএফটি (EFT) পদ্ধতিতে ডিজিটাল এমপিও কার্যক্রম চালু করে।
🔹 এতে বেতন ও ভাতা প্রদানের স্বচ্ছতা, গতি ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।
বর্তমান অবস্থা (২০২4–বর্তমান)
🔹 বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৭,০০০+ এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।
🔹 শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৫ লাখের বেশি।
🔹 সরকার প্রতি বছর প্রায় ৩৫,০০০–৪০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করে বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাবদ।
🔹 বর্তমান সরকার অনলাইন প্রোফাইল, ইএমআইএস ডেটাবেইস ও ইএফটি ব্যাংক ট্রান্সফার চালু করেছে, যাতে:
- মৃত/বরখাস্ত শিক্ষকের বেতন বন্ধ হয়
- তথ্য হালনাগাদ হয়
- ভুয়া এমপিওরোধ সম্ভব হয়
এমপিও ব্যবস্থার প্রভাব
| ইতিবাচক দিক | চ্যালেঞ্জ |
|---|---|
| শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি | অনিয়ম ও ভুয়া তথ্য |
| শিক্ষার মানোন্নয়ন | দেরিতে বেতন ছাড় |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টিকে থাকার সহায়তা | অনুপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত |
| শিক্ষক পেশায় আগ্রহ | তথ্য হালনাগাদে বিলম্ব |
বাংলাদেশে এমপিওভুক্ত ব্যবস্থার ইতিহাস হলো একটি সামাজিক অগ্রযাত্রার গল্প, যেখানে বেসরকারি শিক্ষকদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং জাতীয় শিক্ষার মান উন্নয়নে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তি ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি না ঘটলে এই ব্যবস্থা টেকসই হবে না। এ ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতা বজায় রাখতে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা, তথ্য হালনাগাদ এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা অপরিহার্য। সময়োপযোগী সংস্কার ও তদারকির মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও টেকসই করা সম্ভব।


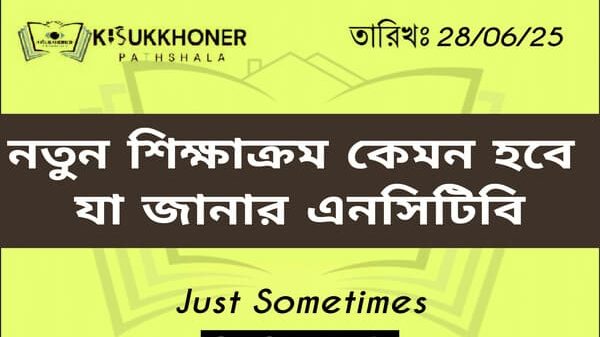
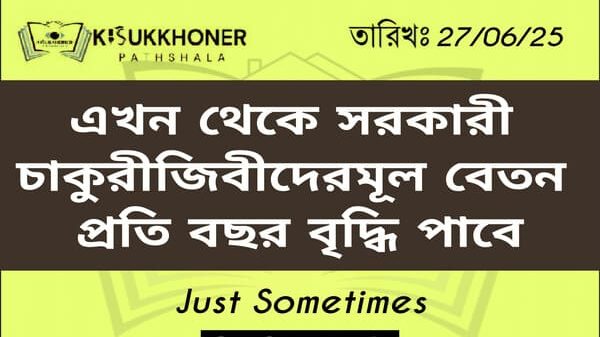
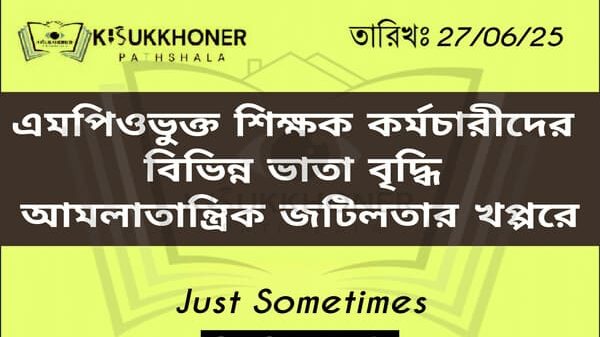
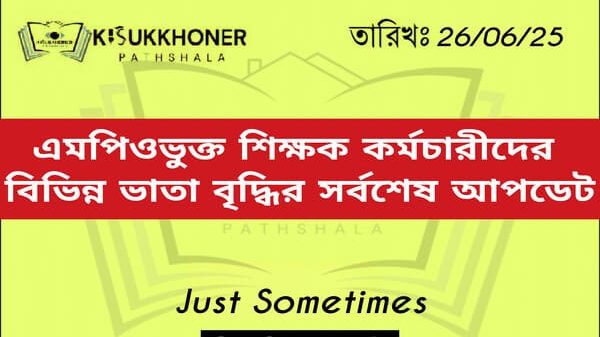
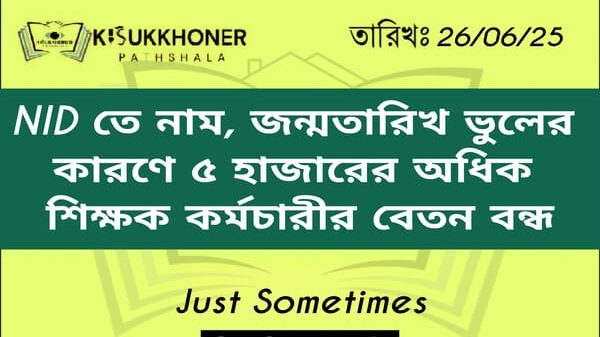
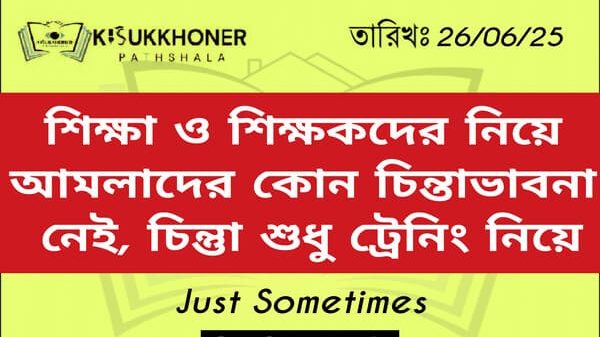
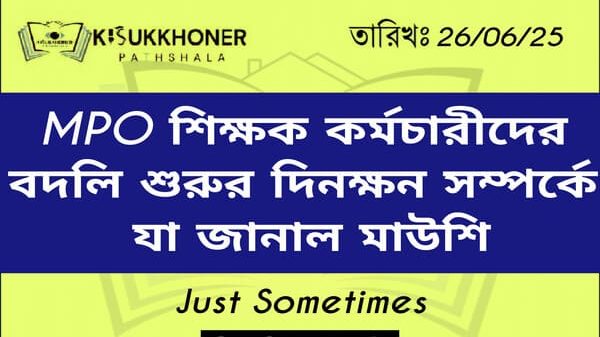
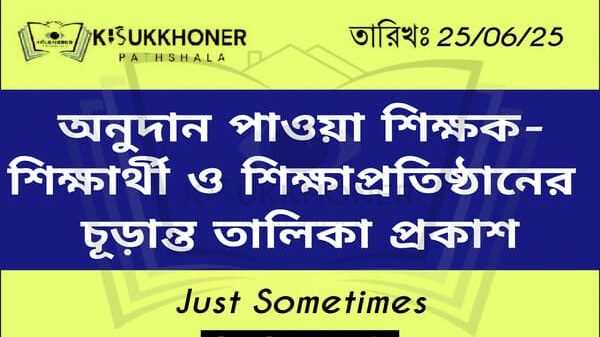
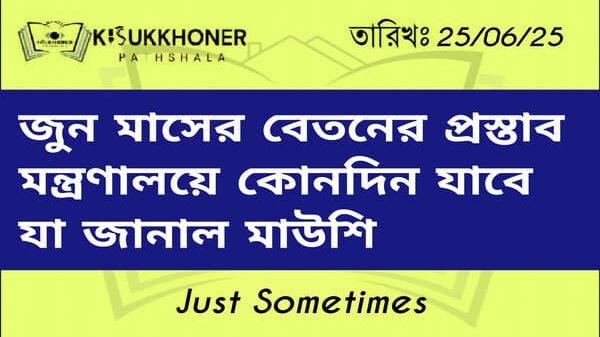
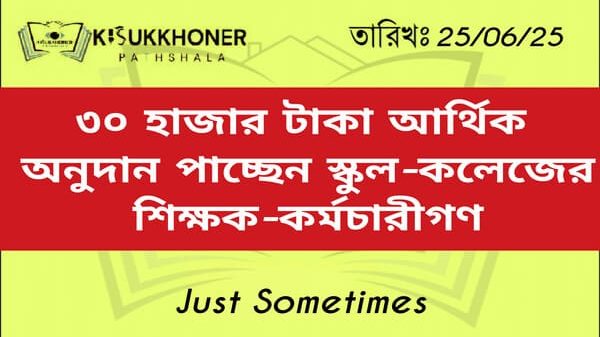
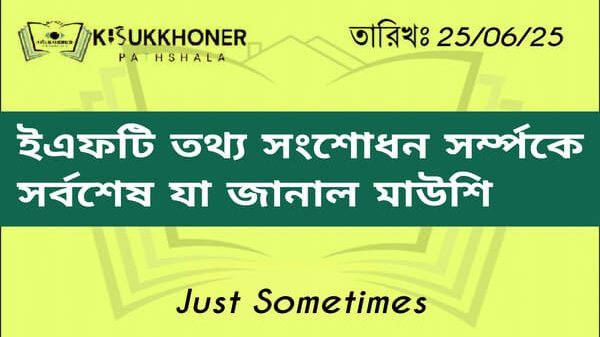

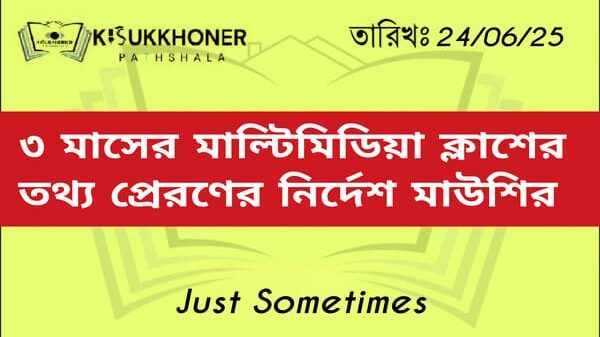
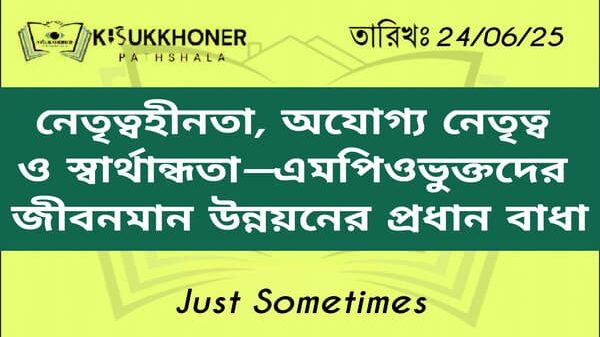
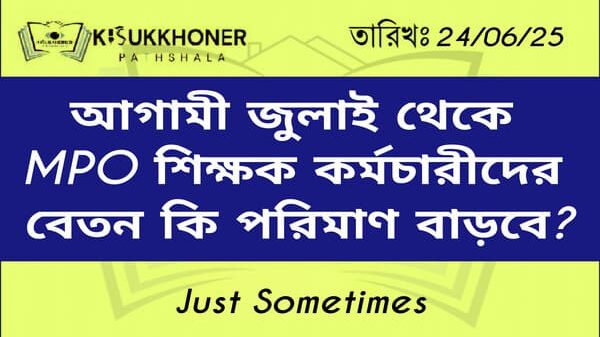
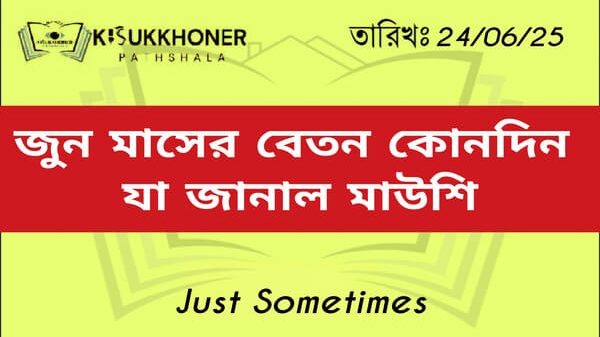
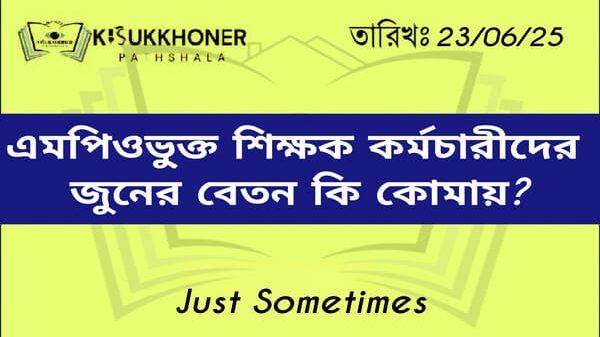
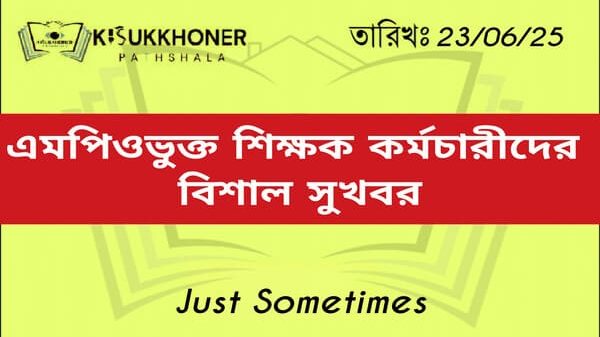
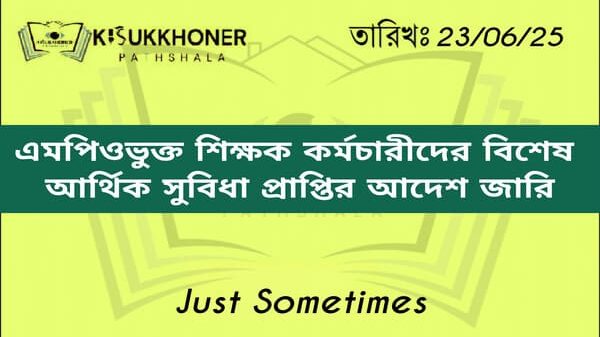
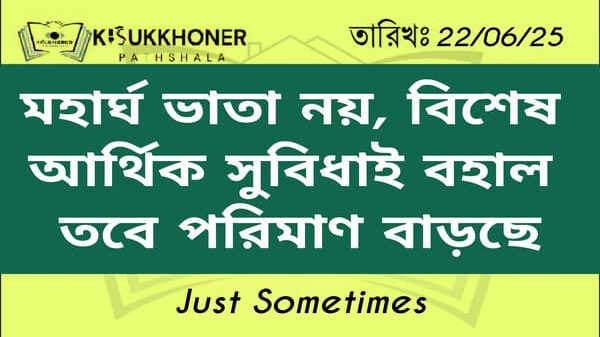
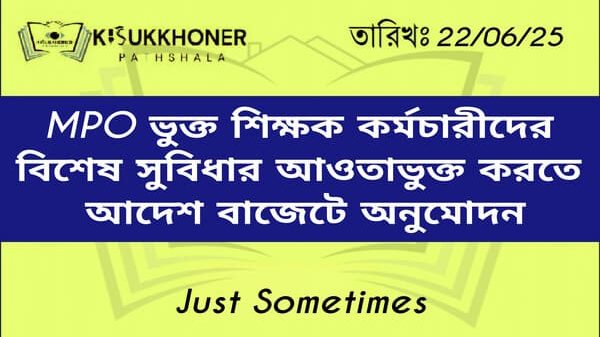
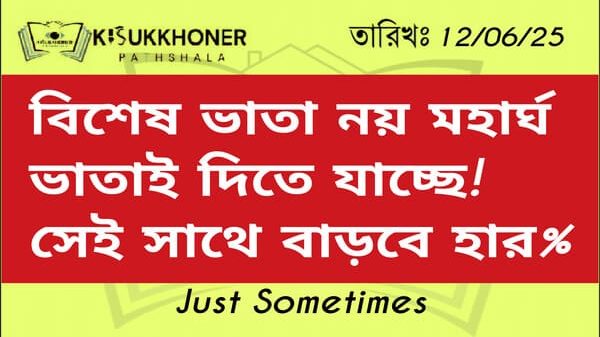
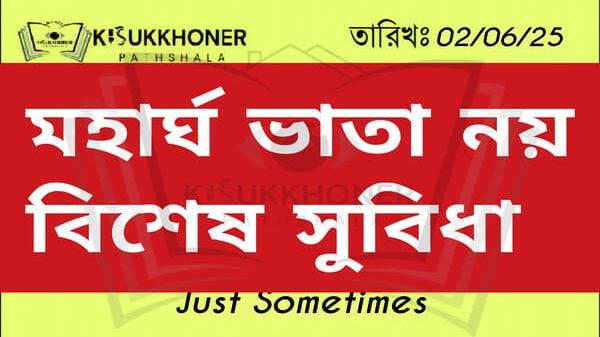
Leave a Reply